প্রিয় পাঠক আজকের বাংলা রচনা পর্বে যে রচনাটি আমরা উপস্থাপন করতে চলেছি তা হল-মহাত্মা গান্ধী প্রবন্ধ রচনা । মাধ্যমিক , উচ্চমাধ্যামিক শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বাংলা প্রবন্ধ রচনা নিয়ে আমাদের আজকের উপস্থাপনা । এছাড়াও পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর রচনা তোমরা পেয়ে যাবে এই পেজে , মহাত্মা গান্ধী উপর 1000 শব্দের রচনা ।
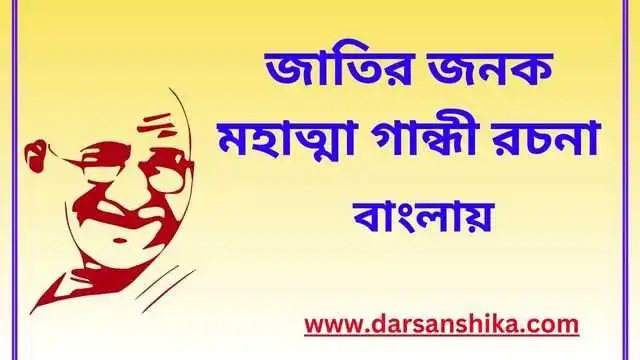
জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী রচনা
ভূমিকা :
“পৃথিবীর সেই সব সত্য অনুসন্ধানের দিনে
বিশ্বের কারণ শিল্পের অপরূপ আভার মতন
আমাদের পৃথিবীর হে আদিম ঊষা পুরুষেরা ,
তোমরা দাঁড়িয়েছিলে,মনে আছে, মহাত্মার ঢের দিন আগে ।“–জীবনানন্দ দাশ ।
পরাধীন ভারতের শাসকের বন্ধাহীন অত্যাচার, শোষণের নব নব ছদ্মবেশ, অসহায়-নিপীড়িত মানুষের প্রতিকারহীন ক্রন্দনরোল, বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনীতি, রাজনীতির এই রঙ্গমঞ্চে এক মহান নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। ভারতের দিকে দিকে তখন প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ শক্তির অপ্রতিহত গতি, কুটির-শিল্পের আসন্ন মৃত্যুধ্বনি, আদর্শভ্রষ্টতা, পরাধীনতার নিরন্তু অন্ধকারে নিমগ্ন মানুষ, ধূমায়িত অসন্তোষ, মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ।জাতির সেই অন্ধকারময় দুঃসময়ে মুক্তির বার্তা নিয়ে এলেন যিনি তিনি হলেন বিশ্ব বরেণ্য মাহাত্মা গান্ধী।
দিশেহারা পথভ্রান্ত মানুষকে দীক্ষিত করলেন নবজীবনের মহামন্ত্রে। ভারতবর্ষের আপামর জনতাকে তিনি জাতীয়তাবোধের প্রবল উন্মাদনায় মাতিয়ে তুললেন। সেই নবজাগ্রত জাতির হাতে তিনি তুলে দিলেন এক অমোঘ অস্ত্র, সে অস্ত্রের নাম ‘অহিংসা’ ।
জন্ম ও বংশপরিচয় :
১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে ভূমিষ্ঠ হলেন ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী। বাল্য নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। পিতা করমচাঁদ উত্তমচাঁদ গান্ধী, মাতা পুতলীবাঈ। তাঁর পূর্বপুরুষরা একসময় মুদির ব্যবসা করতেন। গান্ধীজীর প্রপিতামহ নিজের বুদ্ধি ও যোগ্যতায় দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান হয়েছিলেন। পিতামহও ছিলেন দেওয়ান। পিতা করমচাঁদ গান্ধীও পোরবন্দরে দেওয়ানি করতেন। পরিবারিক আদর্শের বেদীমঞ্চেই তাঁর মহৎজীবনের দীক্ষা।
চরিত্র :
পিতার তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা ও বুদ্ধি এবং মাতার ধর্মপ্রাণতা, ব্রতাচারের নিষ্ঠা, ক্ষমা-করুণা- সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবিক’ গুণ তিনি উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ গল্প কথার আদর্শ নায়ক-নায়িকারাও ছিল তাঁর চরিত্র গঠনের নেপথ্য উৎস।
তিনি বিশ্ব বরেণ্য এমন এক রাজনৈতিক নেতা যিনি রক্তের বদলে রক্ত চাইলেন না। আঘাতের প্রত্যুত্তরে প্রত্যাঘাতের কথাও বললেন না। তাঁর কণ্ঠে ভারত-আত্মার শাশ্বত সুরই প্রতিধ্বনিত হলো। তিনি চাইলেন মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করতে। চাইলেন, আত্মত্যাগের মহানব্রতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে। তাঁর অহিংসার নীতি দুর্বলের মুখোশ নয়, নয় ভীরুর নিরুপায় হুংকার। এই নীতি দুর্জয় শক্তি সাধনা। মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে তা বলিষ্ঠ, সত্যবোধের জাগরণে তা মহিমময়।
পৃথিবীতে মানুষে মানুষে অসাম্য-বৈষম্য ,অন্যায় , অবিচার দূর করতে তিনি সর্ব প্রকার চেষ্টা করেছিলেন । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সর্ব প্রকারের রাজনৈতিক কুলষতা মুক্ত করা , মানুষের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি সঞ্চারিত করা । ব্যক্তিগতভাবে গান্ধিজি ছিলেন ন্ম্র-ভদ্র, সহজ-সরল ও সন্ন্যাসী-সুলভ । নিজের দোষত্রুটির প্রতিকার ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে গান্ধিজির আন্তরিক উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য ।
শিক্ষা জীবন :
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন গান্ধীজি। কুড়ি বছরের নবীন যুবক। ব্যারিস্টারি পড়তে গেলেন বিলেতে। আইনের পঠন-পাঠনের অবসরে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেন বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থাদি। ১৮৯১ সালে ব্যারিস্টারি পাস করে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশে। বোম্বে হাইকোর্টে যোগ দিলেন। এখানেই তাঁর কর্মজীবনের শুরু। অসত্য, মিথ্যাচারের মামলা তিনি পরিহার করতেন।
রাজনৈতিক জীবনের সূচনা :
১৮৯৩ সালে মামলার প্রয়োজনে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে গিয়েছিলেন । সেখানেও ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব। পরাধীন কালা আদমির ওপর চলে পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুর অত্যাচার, দাম্ভিক শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নগ্ন বর্বরতা। দিন দিনই বেড়েই চলেছিল, ভারতীয় বণিক ও শ্রমিক শ্রেণীর ওপর অমানুষিক নির্যাতন। গান্ধীজি এই অপমানিত, মানহারা মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন।
মানবতার জ্বলন্ত শিখায় তিনি দীপ্ত হয়ে উঠলেন। নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন । অনুভব করলেন সশস্ত্র ইংরেজ শক্তির মোকাবিলার জন্যে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তা। গড়ে তুললেন ‘নাটাল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস’। এই প্রতিষ্ঠানই হলো নিষ্পেষিত, নির্যাতিত প্রবাসী ভারতীয়দের মর্যাদা আদায়ের সংগ্রামের হাতিয়ার।
নাটালই হলো তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম কর্মক্ষেত্র। শুরু হলো আপসহীন আন্দোলন। অত্যাচারিত ভারতীয়দের নেতৃত্ব দিলেন নিরস্ত্র গান্ধী। তিনি প্রহৃত হলেন, হলেন কারাবন্দী। তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নাটাল সরকার শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের দাবি মেনে নিল। অহিংসার অস্ত্র প্রয়োগে তিনি সফল হলেন।
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব :
১৯১৫ সালে বিজয়ীর সম্মান নিয়ে গান্ধীজী দেশে ফিরলেন। ইতিমধ্যেই তিনি সঞ্চয় করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অদম্য সেনা নায়কের অভিজ্ঞতা। তাঁর অধিকারে রয়েছে অহিংসার মহাস্ত্র। তিনি বুঝেছিলেন, আপামর জনসাধারণই প্রকৃত শক্তির উৎস। জন জাগরণ তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তারপর যথা সময়েই তাদের হাতে তুলে দিতে হবে সেই অব্যর্থ অস্ত্র। শত শত কামানের গর্জন তখন স্তব্ধ হয়ে যাবে উত্তাল, নিরস্ত্র, জাগ্রত জনতার সামনে। সবরমতী নদী তীরে গড়ে তুললেন এক আদর্শ সেবা প্রতিষ্ঠান। ১৮৮৫ সালেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন হয়েছে।
ভারতের নানা প্রান্তে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধছিল। কংগ্রেসের পতাকা তলে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল মুক্তিকামী মানুষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণডঙ্কা বেজে উঠল। অসহায় ইংরেজ ভারতীয়দের সাহায্য প্রার্থী হলো।
বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি দিল যুদ্ধান্তে ভারতীয়দের হাতে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার অর্পণের কথা । কিন্তু যুদ্ধ শেষে তাই স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে ভারতবাসী পেল ‘রাওলাট আইন’। ভারতের নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হলেন। ১৯২২ সালে জাতীয় কংগ্রেস শুরু করল অসহযোগ আন্দোলন নেতৃত্ব দিলেন গান্ধীজি।
ইংরেজ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম :
ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিনি কামান ,বন্দুকের ব্যবহার করেননি , তিনি অহিংসাকেই তাঁর হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন । ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে দেশময় এলো নবজাগরণের জোয়ার। বিক্ষিপ্ত ইংরেজ বিদ্বেষ গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিলো।গান্ধীজি এই জন জাগরণের প্রয়োজনীয়তাই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশবাসীকে স্বদেশী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে।
গান্ধীজির স্বদেশিকতা :
গান্ধীজি ব্রিটিশ সরকারকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে বিদেশি পণ্য বৈকটের দাবী জানান , গ্রামে গ্রামে মানুষকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনেই তিনি খাদি ও চরকা কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই আদর্শবাদী সংগঠক। তিনি চেয়েছিলেন নিরস্ত্র, উত্তাল, জাগ্রত জনশক্তি দিয়েই দুর্ধর্ষ ইংরেজ শক্তিকে প্রচণ্ড আঘাত হানতে। ১৯৩০ সালে তিনি শুরু করলেন ‘লবণ সত্যাগ্রহ’ আন্দোলন। ইতিহাসে তা ‘ডাণ্ডি অভিযান’ নামে স্মরণীয় হয়ে আছে।
ভারতের জনমনে সৃষ্টি হলো উত্তাল তরঙ্গ। সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনী নিরস্ত্র সংগ্রামের এই সেনা নায়ককে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কিছুদিন পর ইংল্যান্ডে, একবার নয় তিন তিনবার বসল ‘গোলটেবিল বৈঠক।’ উদ্দেশ্য ভারতকে ‘স্বরাজ’ দেবার সূত্র আবিষ্কার।
প্রতিবারেই সেখানে ডাক পড়ল গান্ধীজির। ইংরেজের দুরভিসন্ধিতে প্রতিবারেই হতাশ হয়ে তিনি সভা ত্যাগ করলেন। এবার আরও বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি নিলেন তিনি বিশ্বজুড়ে আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠল। ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট , গান্ধীজি ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তামাম ভারতবাসী সামিল হলো সেই সংগ্রামে। গান্ধীজি কারাবন্দী হলেন। উত্তাল জনতরঙ্গে কেঁপে উঠল ইংরেজ-শাসনের ভিত।
স্বাধীনতা লাভ ও দেশভাগ :
অসহযোগ আন্দোলনের অনিবার্য ফল হলো ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, স্বাধীন ভারত। কিন্তু তার অনেক আগেই ইংরেজ সরকার অখণ্ড ভারতের মাটিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছিলেন। কালে কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পরিণত বৃক্ষে আত্মপ্রকাশ করল। ১৯৪৬ সালে নৃশংস সাম্প্রদায়িকতা হলো সেই বিষফল। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলো , জন্ম নিল ভারত ও পাকিস্তান নামের দুইটি ভূখণ্ড । কিন্তু গান্ধীজি তা চাননি। তাই এ দিনটি তাঁর কাছে ছিল গভীর বেদনার ।
পরলোকগমন :
১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী শান্ত পদে অহিংসার মূর্ত বিগ্রহ এই মহানায়ক চলেছেন প্রার্থনা সভায়। নাথুরাম গডসে নামক মৌলবাদীর হাতে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে, সেখানেই লুটিয়ে পড়লেন। আধুনিক ভারতের এক উজ্জ্বল তারকা এমনি করেই মানুষের ক্ষমাহীন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন।
এখানে আমরা লড়েছি ,মরেছি , করেছি অঙ্গিকার,
এ মৃতদেহের বাঁধা ঠেলে হব অজেয় রাজ্য পার ।
এসেছে বন্যা, এসেছে মৃত্যু , পরে যুদ্ধের ঝড় ,
মন্মন্তর রেখে গেছে তাঁর পথে পথে স্বাক্ষর। -সুকান্ত ভট্টাচার্য ।
উপসংহার :
গান্ধীজি ছিলেন সনাতন ভারত-ঐতিহ্যের আধুনিক বিগ্রহ। তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল সত্য, প্রেম ও অহিংসা। তাঁর মতে –“অহিংসা পরম ধর্ম । সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব না হলে , আমাদের অনন্ত এর ধারণাকে গ্রহণ করা উচিত এবং মানুষ হিসাবে হিংসা থেকে সংযত থাকা।“
তিনি ছিলেন গণ-জাগরণের প্রাণপুরুষ। তাঁর ঈশ্বরানুরাগ তো মানবপ্রেমেরই ভিন্ন নাম। অস্পৃশ্যতাকে তিনি মনে করতেন পাপ। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, স্বাধীনতার আকাঙক্ষা। ছিলেন লাঞ্ছিত মানবতার মুক্তি-দূত, স্পর্ধিত রাজশক্তির অনমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ছিল বিস্ময়কর সাংগঠনিক প্রতিভা। আদর্শে ছিল অবিচল নিষ্ঠা।
Thanks For Reading : মহাত্মা গান্ধী রচনা বাংলায়
■ অনুসরণে লেখা যায়
মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অহিংস নীতি
সার্ধশতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী রচনা
স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজী
মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বাংলায়
আরো পড়ুনঃ
